প্রশিক্ষণ সহায়িকা
প্রাথমিক অগ্নি নির্বাপন
১।
সংজ্ঞাঃ প্রাথমিক অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদি এবং অগ্নি নির্বানপন সরঞ্জামাদি সম্পূর্ণ আলাদা। নিম্নে আলাদা করে দেখান হইলঃ
২। প্রাথমিক অগ্নি নির্বপন সরঞ্জামাদিঃ ফায়ার বাকেট, ফায়ার হুক, ফায়ার বিটার, কাঁথা, কম্বল, সকল ধরনের বহনযোগ্য অগ্নি নির্বপন যন্ত্র, হোজরীল ইত্যাদি।
৩। অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদিঃ ৭ হইতে ১৪ বার প্রেসারে পানি সরবরাহ করিতে সক্ষম পাম্প / হাইড্রেন্ট, রাইজার, স্প্রিংকলার, ইত্যাদি।
আরো জানতে
শিল্প কারখানার রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ও বিবধ || Industrial Risk Assessment
বড়
অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র যেমন পাম্প, হাইড্রেন্ট ইত্যাদি দ্বারা ছোট আগুন নিভাইতে গেলে আগুনের ক্ষতির চাইতে পানিতে ক্ষতি হবে অনেক বেশী আবার প্রাথমিক অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদি দ্বারা বড় আগুন নেভানো
সম্ভব না। কারণঃ
ফায়ার
বাকেট/হোজরীল দ্বারা বড় আগুন নিভাতে
গেলে বড় আগুনের অতিরিক্ত
তাপে ফায়ার বাকেট/হোজরীলের পানি মূল উপাদানে (হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন) বিভাজিত
হয়ে অগ্নি নির্বাপনের পরিবর্তে অধিক প্রজ্বলনের কাজ করবে। কারন হাইড্রোজেন জ্বলে এবং অক্সিজেন জ্বলতে সাহায্য করে।
আগুন (অগ্নি প্রজ্জ্বলন ও নির্বাপন নীতি )
১।
সংজ্ঞাঃ
আগুন হচ্ছে “দাহ্যবস্তু, অক্সিজেন ও তাপ (পরিমিত)
এ তিনটি উপাদানের সংযোগে বিরতিহীন রাসায়নিক
বিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রজ্জ্বলন প্রক্রিয়া”।
২।
অগ্নি প্রজ্জ্বলন নীতিঃ প্রকৃতপক্ষে
প্রজ্বলনের জন্য চারটি উপাদানের প্রয়োজন। এগুলো নিম্নরূপঃ
ক।
প্রজ্জ্বলনের জন্য দাহ্যবস্তু।
খ।
অক্সিজেন।
গ।
পরিমিত তাপ।
ঘ।
বিরতিহীন রাসায়নিক বিক্রিয়া।
যখনই
এ চারটি উপাদানের সংমিশ্রন ঘটবে তখনই আগুনের উৎপত্তি হবে। আর যতোক্ষন পর্যন্ত
এ চারটি উপাদান প্রজ্জ্বলনে বিদ্যমান থাকবে ততক্ষন আগুন জ্বলতে থাকবে। ইহাই অগ্নি প্রজ্জ্বলন নীতি। অগ্নি প্রজ্জ্বলনে চারটি উপাদানের প্রয়োজন হয় বিধায় বর্তমান
আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যায় ইহাকে প্রজ্জ্বলনের চতুর্ভুজ হিসাবে আখ্যায়িত
করা হয়েছে।
৩।
অগ্নি নির্বপন নীতিঃ অগ্নি প্রজ্জ্বলন নীতি থেকে জানা যায় যে, প্রজ্জ্বলনের জন্য দাহ্যবস্তু, পরিমিত তাপ ও অক্সিজেনের সরবরাহসহ
বিরতিহীন রাসায়নিক বিক্রিয়া অপরিহার্য এবং যতক্ষন এ চারটি উপাদান
প্রজ্জ্বলন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান থাকবে ততক্ষন প্রজ্জ্বলন প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। এ চারটি উপাদানের
যে কোন একটি উপাদান অপসারন বা সীমিতকরণ করতে
পারলেই প্রজ্জ্বলনের চর্তুভূজ ভেঙ্গে যাবে এবং প্রজ্জ্বলন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ আগুন নিভে যাবে। ইহাই হচ্ছে অগ্নি নির্বাপন নীতি। যাহাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
৪।
আগুনের শ্রেণী বিন্যাসঃ দাহ্য বস্তুর প্রকারভেদে এবং অগ্নি নির্বাপন মাধ্যম ব্যবহারের সুবিধার্থে আগুনকে চার শ্রেনীতে ভাগ করা হয়েছেঃ
ক।
শ্রেণী-‘ এ ’। (কঠিন পদার্থের আগুন)
খ।
শ্রেণী-‘ বি ’। (তরল
পদার্থের আগুন)
গ।
শ্রেণী-‘ সি ’। (গ্যাসজাতীয়
পদার্থের আগুন)
ঘ।
শ্রেণী-‘ ডি ’। (ধাতব
আগুন)
ক। শ্রেণী ‘এঃ কঠিন পদার্থের আগুন ‘এ’শ্রেণীর আগুনের পর্যায়ভুক্ত। কঠিন দাহ্য বস্তু হচ্ছে, যার আকার ও আয়তন আছে এবং যাতে জ্বলন্ত অংগারের সৃষ্টি হয়। যেমন- কাঠ, পাট, কাপড়, তুলা কাগজ ইত্যাদি। ‘এ’ শ্রেণীর আগুনের উত্তম নির্বাপন মাধ্যম পানি।
নির্বাপন
মাধ্যমঃ
(১)
দাহ্য বস্তুর প্রকার ভেদে পানি ¯স্প্রে আকারে।
(২)
দাহ্য বস্তুর প্রকার ভেদে পানি ফগ আকারে।
(৩)
দাহ্য বস্তুর প্রকার ভেদে পানি জেড আকারে।
(৪)
বহনযোগ্য রাসায়নিক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ওয়াটার টাইপ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার।
(৫)
আগুনের ঝুঁকি অনুসারে স্বয়ংক্রিয় ¯স্প্রিংকলার, হাইড্রেন্ট, ড্রেনচার, হোজরীল ইত্যাদি স্থায়ী অগ্নি নির্বাপন
ব্যবস্থা।
খ। শ্রেণী -‘বিঃ তরল জাতীয় পদার্থের আগুন ‘বি’ শ্রেণীর আগুনের পর্যায়ভুক্ত। যেমন- পেট্রল, ডিজেল, অকটেন, কেরোসিন, তারপিন, মবিল, পেইন্ট ইত্যাদির আগুন।
নির্বাপন মাধ্যমঃ
(১)
পানি ¯স্প্রে আকারে।
(২)
মেকানিক্যাল ফোম।
(৩)
কেমিক্যাল ফোম / এয়ার ফোম।
(৪)
কার্বন-ডাই-অক্সাইড।
(৫) ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার।
গ।
শ্রেণী -‘সিঃ গ্যাসজাতীয়
পদার্থের আগুন ‘সি’ শ্রেণীর পর্যায় ভুক্ত। যেমন- এল,পি গ্যাস,মিথেন, প্রোপেন, বিউটেন ইত্যাদি গ্যাস এর আগুন।
নির্বাপন মাধ্যমঃ
(১)
গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে।
(২) কার্বন-ডাই-অক্সাইড।
(৩)
ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার।
(৪) পানি ¯স্প্রে এবং জেড আকারে।
ঘ। শ্রেণী- ‘ডিঃ ধাতব আগুন ‘ডি’ শ্রেণীর আগুনের পর্যায়ভুক্ত। ধাতব আগুনে পানি অকার্যকর এবং বিপদজনক। কারন তীব্র তাপে পানি মূল উপাদানে (হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন) বিভাজিত হয়ে বিষ্ফোরন ঘটাতে পারে।
নির্বাপন
মাধ্যমঃ
(১)
গ্রাফাইড পাউডার।
(২)
টেলকম পাউডার।
(৩)
সোডা এ্যাস।
(৪)
লাইম স্টোন এবং ড্রাই সেন্ড।
(৫)
স্পেশাল ফিউজিং পাউডার, টারনারী ইউটেকটিক ক্লোরাইড এবং টারনারী ইউটেকটিক ফ্লোরাইড।
(৬) বালি, ছাই, এসবেস্টস্ ইত্যাদি।
৫।
দাহ্য বস্তুঃ যা দ্বারা দহন ক্রিয়া বা প্রজ্জ্বলন প্রক্রিয়া
সম্পন্ন করা হয় তাকে দাহ্য
বস্তু বলে। অগ্নি প্রজ্জলনের চারটি উপাদানের মধ্যে দাহ্য বস্তু অন্যতম। বর্তমান আধুনিক বিশ্বের আধুনিকায়নে দাহ্য বস্তুর বা জ্বালানীর প্রয়োজনীয়তা
অনস্বীকার্য। কারন দাহ্য বস্তু ছাড়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অচল। ইহা ব্যতীত দেশের সার্বিক উন্নয়নে, যানবাহন চলাচলে, শিল্প কারখানা চলাচলে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে দাহ্য বস্তুর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।
৬।
দাহ্য বস্তুর শ্রেণী বিন্যাসঃ আধুনিক অগ্নি প্রযুক্তি বিদ্যায় ঘনত্ব এবং প্রজ্জ্বলন তাপের তারতম্য অনুসারে দাহ্য বস্তুকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃÑ
ক। টিন্ডার ফুয়েলঃ এ শ্রেণীর দাহ্য বস্তুর ঘনত্ব খুব কম এবং ইহা সহজ দাহ্য পদার্থ। সাধারনত ৭৩ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ইহা জ্বলে। যেমন- পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন, কেরোসিন, পাট, তুলা কিছকিছু কেমিক্যাল ইত্যাদি।
খ।
কিন্ডলিং ফুয়েলঃ- টিন্ডার ফুয়েলের চেয়ে এ শ্রেণীর দাহ্য
বস্তুর ঘনত্ব বেশী এবং ইহা মাঝারী দাহ্য পদার্থ। সাধারনত ৭০ হতে ১৫০
ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপে জ্বলে। যেমন- কাগজ, পাট, তুলা, শোলা, খড়, পাতলা কাঠের টুকরা ইত্যাদি।
গ।
বাল্ক ফুয়েলঃ - সাধারনত ১৫০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রার অধিক তাপে যে সমস্ত কঠিন
দাহ্য বস্তু জ্বলে এবং জ্বলন্ত অংগারের সৃষ্টি হয় সেই সমস্ত
দাহ্যবস্তুকে বাল্ক ফুয়েল বলা হয়। যেমন- কাঠ, বাঁশ, সাইজ কাঠ বা গোল কাঠ
ইত্যাদি।
৭। অগ্নি নির্বাপন পদ্ধতিঃ
প্রজ্জ্বলন নীতির মাধ্যমে জানা যায় যে, অগ্নি প্রজ্জ্বলনের জন্য চারটি উপাদান প্রয়োজন। এ চারটি উপাদানের যে কোন এক বা একাধিক উপাদানকে সরাতে বা সীমিত করতে পারলেই আগুন নিভে যাবে। এ শর্তের উপর নির্ভর করে অগ্নি নির্বাপন পদ্ধতিকে নিম্নরূপ চার পদ্ধতিতে ভাগ করা হয়েছেঃ
ক।
দাহ্য বস্তু সীমিত করন পদ্ধতি।
খ।
অক্সিজেন সীমিত করন পদ্ধতি।
গ।
তাপ সীমিত করন পদ্ধতি।
ঘ।
রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বাধাদান বা অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রকে
বিচ্ছিন্ন করন পদ্ধতি।
ক। দাহ্য বস্তু সীমিত করন অগ্নি নির্বাপনে দাহ্যবস্তু সীমিত করন পদ্ধতি তিনভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে
(১)
আগুনের কাছাকাছি বা পার্শ্ববর্তী দাহ্য
বস্তুকে অপসারনের মাধ্যমে।
(২)
দাহ্য বস্তুর নিকটবর্তী বা পার্শ্ববর্তী আগুন
অপসারনের মাধ্যমে।
(৩)
জ্বলন্ত দাহ্য বস্তুকে ভাগ ভাগ করে ছোট ছোট আগুনকে লাঠি, ডাল বা বিটার দ্বারা
আঘাত করে প্রজ্বলনের
কার্যকারিতা কমিয়ে ফেলার মধ্যমে।
খ।
অক্সিজেন সীমিতকরণ পদ্ধতিঃ
যদিও বায়ুমন্ডলের সর্বত্র অক্সিজেন পূর্ণ তবুও প্রজ্জ্বলিত স্থানে অক্সিজেন প্রবেশ বন্ধ করতে পারলে আগুন নিভে যাবে। কারন অক্সিজেন ছাড়া আগুন জ্বলতে পারে না। ভেজা কাঁথা, ভেজা কম্বল ইত্যাদি দিয়ে আগুন ঢেকে দিয়ে অক্সিজেন প্রবেশ বন্ধ করা সম্ভব। কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ফোম ব্যবহার করে অক্সিজেন অপসারন বা সীমিত করা যায়। তবে যে সমস্ত প্রজ্জ্বলিত দাহ্য বস্তু নিজেই অক্সিজেন সৃষ্টি করতে পারে সেই সমস্ত দাহ্য বস্তুর আগুনে এই পদ্ধতি অকার্যকর।
গ।
তাপ সীমিতকরণ পদ্ধতিঃ
প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে যে হারে তাপের উৎপত্তি হয় যদি বিভিন্ন নির্বাপন মাধ্যম দ্বারা সে তাপ সীমিত করা যায় তবে প্রজ্জ্বলন অবিরত চলতে পারে না। নির্বাপন নীতির এ শর্ত প্রয়োগ করতে হলে প্রথম পদক্ষেপ হবে দ্রুত হারে অগ্নিকান্ড থেকে বর্ধিত তাপ অপসারন করা। পানির তাপ শোষন ক্ষমতা অত্যাধিক এবং আমাদের দেশে পানি সহজলভ্য। যে কারনে অগ্নি নির্বাপন কাজে তাপ সীমিতকরণে সাধারনতঃ পানি ব্যবহার হয়ে থাকে। পানি আগুনে ব্যবহৃত হলে তাপ শোষন করে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক রূপে পরিবর্তন হতে পারেঃ
(১)
তাপ শোষন করে আগুনকে ঠান্ডা করে নিজের তাপ মাত্রা বৃদ্ধি করে।
(২)
বাষ্পে পরিনত হতে পারে।
(৩)
মূল উপাদানে (হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন) বিভাজিত
হতে পারে।
(৪)
প্রজ্জ্বলিত দাহ্য বস্তুর সহিত বিক্রিয়া ঘটাতে পারে।
উপরোক্ত (১) এবং (২) পরিবর্তনের কারনে পানি আগুন নিভাতে পারে কিন্তু (৩) মূল উপাদানে (হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন) বিভাজিত হয়ে অগ্নি নির্বাপনের পরিবর্তে অগ্নি প্রজ্জ্বলনে সহায়তা করে। আর (৪) প্রজ্জ্বলিত দাহ্য বস্তুর সহিত বিক্রিয়া ঘটায়ে বিপদ সৃষ্টি করতে পারে।
ঘ। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বাধাদান বা অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রকে বিচ্ছিন্নকরণ পদ্ধতিঃ- প্রজ্জ্বলনের সময় প্রজ্জ্বলিত দাহ্য বস্তুর উপর ড্রাই-পাউডার/ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার ব্যবহার করলে পাউডার কনা প্রজ্জ্বলিত দাহ্য বস্তুর অনুতে অনুতে প্রবেশ করে অনুর কম্পন রোধ করে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি করে। ফলে অবিচ্ছিন্ন যোগ সুত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে আগুন নিভে যায়।
৮।
অগ্নি কান্ডের কারণ নিম্নরূপঃ
ক।
চুলার আগুন।
খ।
বৈদ্যুতিক গোলযোগ বা সর্ট সার্কিট।
গ।
সিগারেটের জ্বলন্ত অবশিষ্টাংশ।
ঘ।
খোলা বাতির ব্যবহার।
ঙ।
ছেলে মেয়েদের আগুন নিয়ে খেলা করা।
চ।
আতস বাজি বা বাজি পোড়ানো।
ছ।
যন্ত্রাংশের ঘর্ষন।
জ। মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রা।
ঝ।
বজ্রপাতের কারনে।
ঞ।
অগ্নিসংযোগ।
ট।
শিল্প কারখানার বয়লারে চিমনীর স্ফুলিংগ হতে।
ঠ।
শত্রুতামূলক।
ড।
সেবোটেজ (উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে লাগান)।
ন।
উত্তপ্ত ছাই।
ণ।
স্বতঃস্ফুর্ত প্রজ্জ্বলন।
ত। মূলতঃ অসাবধানতাই অগ্নি কান্ডের প্রধান কারন।
৯।
অগ্নি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাঃ
ক।
অগ্নিকান্ডের সংকেত বাজার সঙ্গে সঙ্গে আগুন যেখানেই বা যে সেকশনেই
হোক না কেন সম্পূর্ণ
বিদ্যুৎ বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ-
(১)
বিদ্যুৎ চালু অবস্থায় থাকলে বৈদ্যুতিক ইনস্যুলিসন পুড়ে নতুন করে সর্টসার্কিট হয়ে মূহুর্তের মধ্যে সমস্ত কারখানায় আগুন ছড়িয়ে পরতে পারে।
(২)
ন্যাকেড তারের সংস্পর্ষে এসে অগ্নি নির্বাপক দল বা সাধারন
শ্রমিকের জীবন হানী হতে পারে।
তবে যেহেতু চালু অবস্থায় হঠাৎ করে ডাইং এবং ফিনিশিং বন্ধ করলে কেমিক্যাল, সুতা, কাপড়, রাবার বেল্ট ইত্যাদির ক্ষতি হতে পারে সেহেতু আগুনের সংকেত বাজার সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখিত দুইটি শাখা বাদে অন্য সকল শাখার বিদ্যুৎ বন্ধ করতে হবে এবং উল্লেখিত দুইটি শাখার কোনটিতে আগুন ধরেছে নিশ্চিত হওয়া মাত্র সেই শাখার বিদ্যুৎ বন্ধ করতে হবে।
দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ
বিদ্যুত
বিভাগে কর্মরত কর্মীগণ এই দায়িত্ব পালন
করবেন।
খ।
অগ্নি কান্ডের সংকেত বাজার সঙ্গে সঙ্গে আগুন যেখানেই হোক না কেন এসি
প্ল্যান্ট বন্ধ করতে হবে। কারণ
(১)
বাতাস প্রবাহিত হতে থাকলে উড়ন্ত ডাষ্ট এর সাহায্যে মুহুর্তে
আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে।
(২)
ডাষ্টের সঙ্গে আগুন ভেন্টিলেশন, ডাক্ট লাইন হয়ে ডাষ্ট কালেক্টর ও ড্রাম ফিল্টারে
পৌছে মারাত্বক আকার ধারন করতে পারে।
দায়িত্ব
ও কর্তব্যঃ
(ক)
এসি প্ল্যান্টে কর্মরত কর্মীগণ আগুনের সংকেত বাজার সঙ্গে সঙ্গে এসি প্ল্যান্ট বন্ধ করবেন।
(খ)
প্রাথমিক অগ্নি নির্বাপক দল অগ্নি নির্বাপন
কাজ শুরু করার সাথে সাথে ডাক্ট লাইনের ভেন্টিলেশন দিয়ে যাতে আগুন সহ কোন ডাষ্ট
প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে
বিশেষ খেয়াল রাখবে, সম্ভব হলে ভেন্টিলেশনে ঢাকনা দিবে যাতে ভেন্টিলেশন দিয়ে ডাষ্টের সঙ্গে আগুন প্রবেশ করতে না পারে।
(গ)
যে কোন মেশিনারীতে আগুন ধরলে প্রাথমিক অবস্থাতেই ডিসিপি / সিও টু দ্বারা আগুন
নিভিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। আগুন বড় আকার ধারন
বা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকলে হোজরীল থেকে পানি ব্যবহার করতে হবে।
(ঘ)
কাপড় বা অন্য কোন
কঠিন পদার্থে আগুন ধরলে ডিসিপি, সিও টু ব্যবহারের সাথে
সাথে হোজরীল থেকে পানি ব্যবহার করতে হবে। আগুন বড় হওয়ার বা
ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে হাইড্রেন্ট থেকে লাইন নিয়ে আগুন নিভাইতে হবে।
(ঙ)
সবসময় আগুনের অগ্রযাত্রাকে সামনে রেখে অগ্নি নির্বাপন কাজ শুরু করতে হবে।
(চ)
ফলস্ সেলিং আগুনের সংস্পর্শে এলে দ্রূত ছড়িয়ে যেতে পারে। আগুন বড় হতে দেখলে
আগুন ধরার পূর্বেই ফলস্ সেলিং পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।
(ছ।
ফল্স্ সেলিংয়ে আগুন ধরে গেলে সরাসরি আগুনের নীচে না দাড়িয়ে পাশে
দাড়িয়ে পানি দিতে হবে।
১০।
আগুন বিস্তারের প্রক্রিয়াঃ
প্রজ্জ্বলন
নীতিতে আমরা পেয়েছি তিনটি উপাদান এবং একটি বীরতিহীন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে আগুনের সূত্রপাত ঘটে এবং উপাদান তিনটি যতক্ষন পর্যন্ত সঠিক মাত্রায় সরবরাহ থাকে আগুন ততক্ষন জ্বলতে থাকে। আর প্রজ্জ্বলন প্রক্রিয়াটি
বেড়ে এক সময় আগুনের
বিস্তার ঘটে। প্রজ্জ্বলন প্রক্রিয়ার মূল উপাদান তাপ, আর এই তাপ
সঞ্চালিত হয়ে প্রজ্জ্বলন প্রক্রিয়ার বিস্তার ঘটায়। তাই আগুনের বিস্তার প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালিত হয় তিন পদ্ধতিতে
যেমন -
ক।
পরিবহন।
খ।
পরিচালন।
গ।
বিকিরন।
ক।
পরিবহন
যে
পদ্ধতিতে পদার্থের অনুগুলো তাদের নিজস্ব স্থান পরিবর্তন না করে শুধু
স্পন্দনের মাধ্যমে এক অনু তার
পার্শ্ববর্তী অনুতে তাপ প্রদান করে পদার্থের উষ্ণতর (গরম) অংশ থেকে শীতলতর (ঠান্ডা) অংশে তাপ সঞ্চালিত করে সেই পদ্ধতিকে পরিবহন বলে।
উদাহরণঃ একটি ধাতব দন্ডের এক প্রান্ত আগুনে রেখে অন্য প্রান্ত হাতে ধরে রাখলে কিছুক্ষন পরেই হাতে বেশ গরম বোধ হয়। দন্ডের যে প্রান্ত আগুনের মধ্যে আছে সেই অংশের অনুগুলো আগুন থেকে তাপ গ্রহন করে নিজের অবস্থানে থেকে স্পন্দনের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী ঠান্ডা অনুগুলোকে তাপ প্রদান করে। এভাবে ধাতব পদার্থের এক অনু থেকে অন্য অনুতে তাপ সঞ্চালন করাকেই পরিবহন বলে।
খ।
পরিচালনঃ যে পদ্ধতিতে তাপ কোন পদার্থের অনুগুলোর চলাচল দ্বারা উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে সঞ্চালিত হয় তাকে পরিচালন
বলা হয়। তরল ও বায়বীয় পদার্থের
তাপ এই পদ্ধতিতে সঞ্চালিত
হয়।
উদাহরণঃ
তরল পদার্থ তাপ পেলেই হালকা হয় এবং হালকা
তরল পদার্থ উপরের দিকে উঠে যায়। তখন চারপাশের ঠান্ডা তরল পদার্থ সে স্থান দখল
করে। এ ভাবে চলতে
চলতে তরল পদার্থ অধিক তাপে হালকা হয়ে গ্যাস আকারে সিঁড়ি, লিফট বা দরজা/জানালার
ফাঁকা স্থান দিয়ে উপরে উঠে সে স্থানের দাহ্য
বস্তুকে উত্তপ্ত করে আগুন ধরে দেয়।
গ।
বিকিরনঃ যে
পদ্ধতিতে তাপ জড় মাধ্যমের সাহায্য
ছাড়াই তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গের আকারে উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তুতে সঞ্চালিত হয় তাকে বিকিরণ
বলে।
পরিবহন
ও পরিচালনে তাপ এক স্থান থেকে
অন্যস্থানে সঞ্চালিত হওয়ার জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাপ বিকিরণ পদ্ধতিতে মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। এই
পদ্ধতিতে শূন্য স্থানের মধ্য দিয়ে তাপ সঞ্চালিত হতে পারে।
উদাহরণঃ তাপ শক্তির প্রধান উৎস সুর্য। সুর্য থেকে বিকিরিত তাপ শক্তি প্রধানত “বেন্ড অফ ওয়েব লেন্স” আকারে হয়ে থাকে। যাকে আলো বলা হয়। কারন চোখে ধরা পরে। কিন্তু যে তাপ চোখের অক্ষিপটে ধরা পরে না তা ইনফ্রারেড ওয়েভে বিকিরণ করে। যে পদার্থ তাপ গ্রহন না করে প্রতিফলিত করে তাকে স্বচ্ছ পদার্থ বলে, যেমন কাঁচ। বনে জঙ্গলে স্বচ্ছ কাঁচের মাধ্যমে সূর্যের তাপ প্রতিফলিত হয়ে আগুন ধরে যায়। জানালার কাঁচের মাধ্যমে ঘরে প্রবেশ করে এই তাপ বিকিরিত হয়ে অন্য যে কোন স্থানে এই পদ্ধতিতে আগুন ধরতে পারে।
আরো জানতে
How to write an Appointment Letter In English
বহনযোগ্য রাসায়নিক
অগ্নি
নির্বাপক
যন্ত্র
{প্রটেবল
ফায়ার এক্সটিংগুইসার}
আলোচ্য বিষয়ঃ বহন যোগ্য রাসায়নিক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র বিভিন্ন শ্রেণীর অগ্নি নির্বাপনের উপর ভিত্তি করে সাধারনভাবে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ
ক।
বহনযোগ্য ওয়াটার টাইপ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র।
খ।
বহনযোগ্য ফোম টাইপ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র।
গ।
বহনযোগ্য কার্বন-ডাই- আক্সাইড অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র।
ঘ।
বহনযোগ্য ড্রাই-কেমিক্যাল অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র।
ক।
ওয়াটার টাইপ এবং খ। ফোম টাইপ
এখানে ব্যবহার নাই।
গ।
বহনযোগ্য কার্বন-ডাই- আক্সাইড অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রঃ
(১) সংজ্ঞাঃ সহজে বহন করে যে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের করে প্রজ্জ্বলিত দাহ্য বস্তুর উপর থেকে অক্সিজেন সীমিত করে অগ্নি নির্বাপনে সক্ষম তাকে বহনযোগ্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র বলে।
(২)
গঠনপ্রণালীঃ এ যন্ত্রের সিলিন্ডার স্টীলের তৈরি। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩,৩৭৫ পাঃ
প্রেসারে পরীক্ষিত। সিলিন্ডারের উপরে একটি অপারেটিং লিভার আছে। সিলিন্ডার বহন করার জন্য একটি হাতল, গ্যাস বের হবার জন্য একটি প্রেসার রিলিজ ভাল্ব, উচ্চ চাপ সহনশীল একটি হোজ পাইপ, ধরার জন্য একটি হাতল, গ্যাস স¤প্রসারন হর্ণ,
সিলিন্ডার থেকে গ্যাস বের হবার জন্য একটি ডিস্চার্জ টিউব ও একটি নিরাপদ
পিন থাকে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ৭৩.১ বার
চাপে এবং ৩১.১ ডিগ্রী
সেলসিয়াস তাপ মাত্রায় তরল করে সিলিন্ডারে ভরে রাখা হয়।
(৩) ব্যবহার বিধিঃ অগ্নি নির্বাপন কাজে ব্যবহারের সময় হর্ণটি আগুনের দিকে তাক করে নিরাপদ পিন খুলে প্রেসার রিলিজ লিভারে চাপ দিলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস হর্ণের মাধ্যমে বের হয়ে বাতাসের সংস্পর্শে তরল থেকে গ্যাসীয় আকার ধারন করে খুব দ্রুত গতিতে ঠান্ডা অবস্থার সৃষ্টি করে এবং অক্সিজেনকে সরিয়ে দাহ্য বস্তুর উপর তুষারের আবরণ সৃষ্টি করে আগুন নির্বাপন করবে। ডিসচার্জ রেঞ্চ মাত্র ৩ মিটার এবং নির্গমন সময় ৫ থেকে ৩০ সেকেন্ড মাত্র।
(৪) সুবিধা সমুহঃ
(ক)
এই গ্যাস নন-টক্সিক। এ
গ্যাস নিজে জ্বলে না, অপরকে জ্বলতে সাহায্য করে না।
(খ)
ধাতব পদার্থ ব্যতীত অধিকাংশ পদার্থে প্রতিক্রিয়া করে না।
(গ)
এ গ্যাস নিজস্ব চাপে সিলিন্ডার থেকে বের হয়।
(ঘ)
এ গ্যাস বিদ্যুৎ অপরিবাহী এবং সু² স্পর্শকাতর বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের কোন ক্ষতি হয় না।
(ঙ)
এ গ্যাস পরিস্কার তাই দাহ্য বস্তুর উপরে কোন প্রভাব পরে না।
(চ)
১ লিটার তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রায় ০.৫ কিউবিক
মিটার মুক্ত গ্যাস তৈরি করে। ইহার প্রসারের অনুপাত ৪৫০:১।
(৫)
অসুবিধা সমুহঃ
(ক)
কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস সিলিন্ডার হতে বের হবার সময় খুবই কম। সুতরাং এই স্বল্প সময়ে
পূর্ন সুযোগ গ্রহন করতে না পারলে উদ্দেশ্য
ব্যাহত হবে। একটি ৬.৮ লিটার
ওজনের যন্ত্রের গ্যাস বের হবার সর্বোচ্চ সময় ৩০ সেকেন্ড মাত্র।
(খ)
এ গ্যাস বের হবার সময় হাতে লাগলে কুলবার্ন হতে পারে।
(গ)
বাতাসে এ গ্যাসের ঘনত্ব
৯% এর বেশি হলে
শ্বাসকষ্ট হবে।
(ঘ)
নির্গত গ্যাস বদ্ধ ঘরে ঘন বাস্পের সৃষ্টি
করতে পারে এবং এতে দৃষ্টি শক্তি সীমিত করে দিতে পারে।
(ঙ) খোলা জায়গায় ব্যবহার করলে, অগ্নি নির্বাপনের পূর্বেই এ গ্যাসকে বাতাস ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে।
(চ)
ধাতব আগুনে ব্যবহার করলে এ গ্যাস মূল
উপাদানে বিভাজিত হয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে।
(ছ) এ গ্যাসের
পুনঃপ্রজ্জ্বলন রোধ ক্ষমতা কম। কারন এ গ্যাস দাহ্য
বস্তুকে সম্পুর্ণ ঠান্ডা করতে পারে না।
(৬) রিফিলিং ও রক্ষণাবেক্ষণঃ আগুনে ব্যবহৃত না হলে ১০ বৎসর পর রিফিলিং করতে হবে। প্রতি মাসে ওজন পরীক্ষা করতে হবে। সমগ্র ওজনের ১০% এর বেশি ওজন কম হলে পুনঃভর্তি করতে হবে। হর্ণ এবং ফ্ল্যাক্সিবেল হোজ পাইপ যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে।
ঘ।
বহনযোগ্য ড্রাই-কেমিক্যাল অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রঃ
(১)
সংজ্ঞাঃ
সহজে
বহন করে নিয়ে যে অগ্নি নির্বাপক
যন্ত্র দ্বারা ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার বের করে অগ্নি নির্বাপন করা যায় তাকে বহনযোগ্য ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র বলে।
(২)
প্রকারভেদঃ ড্রাইকেমিক্যাল
অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ২ প্রকার। যথা
-
(ক)
ষ্টোরড প্রেসারটাইপ।
(খ) গ্যাস কার্টিজ
টাইপ।
(৩)
গঠন প্রনালীঃ ড্রাই কেমিক্যাল অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের সিলিন্ডার মাইল্ড স্টীলের তৈরী এবং ইহা প্রতি বর্গ
ইঞ্চিতে ৩৫০ পাউন্ড প্রেসারে পরীক্ষিত। সিলিন্ডারের মুখ ক্যাপ দ্বারা আটকানো থাকে। ক্যাপের সাথে একটি লিভার বা ট্রিগার আছে
এবং উহাতে নিরাপদ পিন লাগান থাকে। গ্যাস কার্টিজ টাইপে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস সিলিন্ডারের মধ্যে বের হবার জন্য একটি টিউব এবং সিলিন্ডারের মধ্য হতে পাউডার বের হবার জন্য একটি ডিসচার্জ টিউব আছে। ষ্টোরড প্রেসার টাইপে পাউডার বের হবার জন্য একটি মাত্র ডিস্চার্জ টিউব আছে। ডিস্চার্জ টিউবের মাথায় একটি হোজ পাইপ এবং হোজ পাইপের মাথায় একটি নজল আছে।
(৪)
ব্যবহার বিধি ও কার্যকারিতাঃ এ
অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র ব্যবহারের সময় এর নিরাপদ পিন
খুলে ট্রিগারে চাপ দিলে পাইডার হোজ পাইপ এবং নজলের মধ্য দিয়ে বের হয়ে দাহ্য বস্তুর উপর পড়ে দাহ্য বস্তুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বাধা প্রদান করতঃ বিরতিহীন রাসায়নিক বিক্রিয়া বা অবিচ্ছিন্ন যোগসুত্র
বিচ্ছিন্ন করে অগ্নি নির্বাপন করে।
(৫)
পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষঃ কোম্পানি থেকে প্রাপ্তির তিন মাস পর পর পরীক্ষা
করে দেখতে হবে :-
(ক)
যন্ত্রটি ওজন করে দেখতে হবে পাইডারের পরিমান ঠিক আছে কিনা।
(খ)
পাউডার নেড়ে দেখতে হবে জমাট বেঁধে গেছে কি না ?
(গ)
গ্যাস কার্টিজ ওজন করে দেখতে হবে ১০% এর বেশি কম
হয়েছে কিনা ?
(ঘ)
প্রেসার টাইপে প্রেসার ইন্ডিকেটর সঠিক আছে কিনা ?
(ঙ)
নজল হোজ পাইপ ইত্যাদি পরিস্কার রাখতে হবে।
(চ)
যন্ত্রের ভিতরে এবং বাইরে কোন ক্ষয় হয়েছে কিনা ?
(ছ) মান অনুযায়ী ১/২ বৎসর পর সম্পূর্ণ ডিসচার্জ করতঃ পরীক্ষা করিয়া পুনঃ ভর্তি করতে হবে।
ডাষ্ট বা
ধূলি কনার আগুন
১।
ভূমিকাঃ বড় উৎপাদনশীল প্ল্যান্টে সূ² ধূলিকণা বা পাউডার বা
আঁশ ঘনীভূত আকারে ভাসমান অবস্থায় কিংবা কখনো ছোট ছোট স্তুপ আকারে বিদ্যমান থাকে। এরূপ ধূলিকণা তাপ, অক্সিজেন এর সংস্পর্শে এসে
বিস্ফোরন ঘটিয়ে অগ্নিকান্ড সৃষ্টি করে।
২।
ডাষ্ট বিস্ফোরনের প্রকার নিম্নরূপঃ
ক।
ডাষ্ট পার্টিকেলস অতি দ্রূত প্রজ্জ্বলিত হয়ে ডাষ্ট বিস্ফোরন ঘটাতে পারে।
খ।
কিছু কিছু ডাষ্ট ধীর গতিতে প্রজ্জ্বলিত হয়ে বিস্ফোরন ঘটাতে পারে। এ প্রজ্জ্বলন শিখাবিহীন
হয়ে থাকে। ডাষ্টের আগুন বিস্ফোরন তীব্রতা অধিক এবং দ্রুত প্রজ্বলিত হয়।
৩।
ডাষ্ট মেঘঃ
ডাষ্ট কণাসমুহ ঘণীভূত আকারে ডাষ্ট ক্লাউডস্ বা ডাষ্ট মেঘ তৈরি হয় যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এরূপ মেঘ বাতাসের সংস্পর্শে এসে ভয়াবহ আগুন সৃষ্টি করে ভবনসমুহ, স্থাপনা বা প্ল্যান্ট, খোলা জায়গা প্রভৃতিতে অগ্নি কান্ড ঘটিয়ে জীবন ও সম্পদহানী করে।
৪।
ডাষ্ট পরিষ্কারকরণঃ
ডাস্ট ক্লাউডকে যদি নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা বাতাসের চাপ প্রয়োগ করে দরজা, জানালা ও ভেন্ট দিয়ে নিয়মিত বের করে দিয়ে স্থাপনাকে ডাষ্ট মুক্ত করে ধুলি বিস্ফোরণের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব।
৫।
ডাষ্ট বিস্ফোরণের কারনঃ
ক।
মেশিনে গ্রাইন্ডিং/চুর্ণ করার সময় মিল কারখানায় প্রচুর পাউডার তৈরি হয় এবং ধুলি
বা পাউডার নিস্কাশনের সময় মেশিনে ডাষ্ট এক্সপ্লোশন হয়ে থাকে। মেশিনের যে অংশে ডাষ্ট
জমা হয় তাকে সাইক্লোন
বলে।
খ।
এসব গ্রাইন্ডিং মেশিন সাধারনতঃ বেষ্টনীকৃত থাকে। ফলে সেখানে প্রচুর ডাষ্ট জমা হয় । ডাষ্ট
নিস্কাশনের সময় ডাষ্ট বা নালীপথ এবং
সাইক্লোনে ফ্রিকশন বা বৈদ্যুতিক তার
কিংবা মটর অতিরিক্ত গরম হয়ে স্থির বিদ্যুত থেকে স্পার্ক সৃষ্টি করে এক্সপ্লোশন হয়।
গ।
কয়লা, রাবার ও জিংক সালফেট
এর ডাষ্ট স্বতঃস্ফর্ত আগুন সৃষ্টি করতে পারে।
ঘ।
যুদ্ধকালীন সময় কলকারখানার উপরে বা নিকটে তীব্র
বিষ্ফোরক বোমা পড়লে মুহুর্তে ডাষ্ট ক্লাউড বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরতে পারে।
ঙ।
হ্যাজার্ডাস শিল্প কারখানায় কিছু কিছু ডাষ্ট থাকে যাতে আগুন বা বিস্ফোরন হতে
স্বল্প তাপ প্রয়োজন হয়।
৬।
প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাঃ ভয়াবহ ডাষ্ট এক্সপ্লোশন এর ঝুঁকি নিম্নে
উল্লেখিতভাবে কমানো যায়।
ক।
স্থাপনার ভবনাদী বা কারখানার অবকাঠামো
সঠিকভাবে নির্মাণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন
রাখা এবং ডাষ্টমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা।
খ।
কারখানার গ্রাইন্ডিং ও সাইক্লোন মেশিনসমুহ
ভাল আচ্ছাদন বেস্টিত করা যাতে ডাষ্ট ঘনীভূত হতে না পারে এবং
যত্রতত্র ছরাতে না পারে। প্ল্যান্টের
ভবনের কক্ষে ডাষ্ট ছড়িয়ে বা জমিয়ে ছোট
ছোট স্তুপ সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য
পর্যাপ্ত ভেন্ট থাকতে হবে এবং ইনার্ট গ্যাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
গ।
যেখানে তুলা বা তুলাজাত দ্রব্য,
পাট বা পাটজাত দ্রব্য
প্রসেস করা হয় এবং আটা,
ময়দা, চাউল, ভুট্টা ইত্যাদি
খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় সেখানে ফায়ার
এলার্ম ও ডিটেকশন সিষ্টেম
এবং ¯স্প্রিংকলার সিষ্টেম থাকতে হবে যাতে আগুনের সুত্রপাতেই সন্ধান পাওয়া যায় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিভে যায় বা তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা
গ্রহন করিয়া আগুন নেভানো যায়।
৭।
পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও ডাষ্ট আগুন
নির্বাপনের মাধ্যম নিম্নরূপঃ
ক।
ডাষ্ট ফায়ার ফাইটিং এর সময় ফায়ারম্যানদের
জানতে হবে কোন ধরনের ডাষ্ট এর মধ্যে আগুন
জ্বলছে এবং এ আগুনে কি
ধরনের ঝুঁকি আছে।
খ।
অগ্নিকান্ডস্থলে ডাষ্টের স্তুপ থাকলে পানির জেট দেয়া যাবে না। কারন পানির স্পীডে এ ডাষ্ট আলোড়িত
হলে বিস্ফোরন ঘটাতে পারে। নিম্ন গতিতে স্প্রে দিয়ে হালকা পানি প্রয়োগ করে আগুন নিভাতে হবে।
গ।
সতর্কতার সাথে ডাষ্ট ক্লাউড এড়িয়ে অগ্নি নির্বাপন করতে হবে।
ঘ।
মেটাল ডাষ্ট ফায়ারে ফোম, ভ্যাপারাইজিং লিক্যুইড ও পানি ব্যবহার
করা যাবে না। ডিসিপি, টেলকম পাউডার, এসবেসটস পাউডার, শুকনো বালি, গ্রাফাইট, ছাই দিয়ে আগুন নিভাতে হবে।
ঙ।
নাড়াচাড়া বা স্থানান্তর করা
যাবে না এমন কার্টুন,
ড্রাম, খোলা কন্টেইনার ইত্যাদিতে জমে থাকা ডাষ্টের আগুন নিভাতে হলে সেখানে পানির বন্যা বইয়ে দিতে হবে।
চ।
কোন কোন ডাষ্টের আগুনে হাই-এক্সপানশন ফোম ব্যবহার করা যেতে পারে।
নতুন নিয়োগকৃত শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রশিক্ষন ও বিস্তারিত আলোচনা || New Employee orientation training
স্থায়ী অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা
১। সংজ্ঞাঃ নিজস্ব সম্পদ বা মালামাল অগ্নিকান্ডের কবল হতে রক্ষার্থে যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বীয় উদ্যোগে আগুনের ঝুকি অনুসারে পূর্ব থেকে স্বয়ংক্রিয় বা অস্বয়ংক্রিয় কোন স্থায়ী ব্যবস্থা তৈরি করে তবে তাকে স্থায়ী অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা বলে।
২।
প্রকার ভেদঃ স্থায়ী অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাকে ২ ভাগে ভাগ
করা হয়েছে। যথা -
ক।
নির্বাপন মাধ্যম -পানি।
(১)
এক ইউনিট প্রতিরোধ ব্যবস্থা।
(২)
¯স্পিংকলার ব্যবস্থা।
(৩)
হাইড্রেন্ট।
(৪)
হোজরীল।
(৫)
রাইজিং মেইন/স্টান্ড পাইপ।
(৬)
স্টীম।
(১)
এক
ইউনিট প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ প্রতি ২৫০ বর্গফুটের জন্য এ ব্যবস্থা। ৯
লিটার ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ৩ বালতি পানি
কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করে রাখা। বালতির উপরিভাগ লাল রং দ্বারা আবৃত
থাকবে এবং সাদা রং দ্বারা “আগুন”
কথাটি লিখা থাকবে।
(২) স্প্রিংকলার, ব্যবস্থাঃ একে ৩ ভাগে ভাগ
করা হয়েছে। যথাঃ
(ক)
¯ স্প্রিংকলারঃ বাড়ী ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কলকারখানা ইত্যাদির ভিতরের আগুনে পানি দিয়ে নির্বাপনের একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা।
(খ)
ড্রেঞ্চারঃ বাহিরের কোন উৎস থেকে আগুন এসে যাতে প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পরতে না পারে তার
জন্য স্বয়ংক্রিয় বা অস্বয়ংক্রিয় এ
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
(গ) ওয়াটার ¯স্প্রে সিষ্টেম প্রজেক্টরঃএ ব্যবস্থায় বিশেষ ধরনের স্প্রিংকলার হেড সংযোজন করে পানিতে মিশে না এমন ধরনের দাহ্য ব¯তুতে পানি ব্যবহার করে আগুন নির্বাপন করা যায়। ইহা দ্বারা স্বয়ংক্রিয় বা অস্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করা যায়।
স্প্রিংকলার
মূলনীতিঃ স্প্রিংকলার ভবনের
সকল স্থানে সিলিং - এর নিকটে পাইপ
লাইন দিয়ে এমনভাবে সজ্জিত করতে হবে যাতে সকল স্থানই সুরক্ষিত হয়। সাধারনভাবে পাইপ লাইনের মধ্যে ১০ ফুট দুরে
দুরে ¯ স্প্রিংকলার হেড বসাতে হয়। একটি স্প্রিংকলার হেড ১০০
বর্গফুট মেঝেতে পানি ছড়িয়ে দিতে পারে। পাকা ভবনে স্প্রিংকলার পাইপ সিলিং থেকে ১৮ ইঞ্চি এবং
কাঁচা ঘরে ১২ ইঞ্চি দুরে
স্থাপন করতে হয়। ভবনের বাহিরে পাইপ লাইনের সাথে গংবেল স্থাপন করা থাকে,যাতে পানি প্রবাহের সময় বেল বাজিয়ে আগুনের সংবাদ জানিয়ে সতর্ক করে দিতে পারে।
স্প্রিংকলার
বৈশিষ্ট্যঃ
ইহা
আগুনের নির্দেশক।
ইহা
শব্দ করে।
ইহা
আগুনকে আক্রমন করে।
ইহা
আগুনকে সীমাবদ্ধ রাখে।
(৩) হাইড্রেন্টঃ পানির উৎসস্থল থেকে কারখানা এলাকার চতুর্দিকে বা যে এলাকার
অগ্নি নির্বাপনের জন্য হাইড্রেন্ট স্থাপন করা হবে সেই এলাকার রাস্তার পাশে মাটির নিচ দিয়ে পাইপ লাইন বেষ্টিত করা হয়। দীর্ঘ পাইপ লাইনের মাঝে ঝুকি অনুযায়ী ৬০ মিটার থেকে
১৮০ মিটার পর পর হাইড্রেন্ট
পয়েন্ট স্থাপন করা হয়। হোজরীল পয়েন্ট থেকে হোজ পাইপ সংযোগ দিয়ে অগ্নি নির্বাপনের জন্য নির্ধারিত সমগ্র এরাকাতে নেওয়া যায় এমন সংখ্যক হোজ পাইপ হোজরীল পয়েন্টে সংরক্ষন করতে হবে। পাইপ লাইনে সবসময় পানির চাপ রাখার জন্য একটি যোকি পাম্প এবং কাজের সময় পানির চাপ বৃদ্ধির জন্য ১ টি সহযোগী
ও ১ টি বিকল্প
পাম্প বসানো থাকে। যোকি পাম্পের সাহায্যে পাইপ লাইনে পানির চাপ দিয়ে রাখার ফলে হাইড্রেন্ট পয়েন্টে ডেলিভারী হোজ পাইপ লাগিয়ে হুইল খুলে দিলেই পানি সরবরাহ পাওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে যোকি পাম্প এবং প্রয়োজন অনুযায়ি সহযোগী পাম্প স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে পানির চাপ অব্যাহত রাখে। হাইড্রেন্ট পয়েন্ট থেকে সামান্য ২/১ টি
ডেলিভারী হোজ পাইপ খুলে হুইল খুলে দিলেই পানির চাপ ও প্রবাহ সঠিক
পাওয়া যায় বিধায় হাইড্রেন্ট অগ্নি নির্বাপনের জন্য খুবই উপযোগী।
(৪) হোজরীলঃ প্রতিটি হোজরীল ১০০ ফুট বা ৩০ মিটার
লম্বা। হোজরীল এমন সংখক স্থাপন করতে হবে যাতে প্রত্যেক প্রকোষ্টের প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে। হাইড্রেন্ট এর মতই হোজরীলে
পানি সরবরাহ ব্যবস্থা থাকে। হোজরীল পাইপ চিকন ও পানির প্রেসার
কম থাকায় ইচ্ছা অনুযায়ী শুধুমাত্র আগুনে পানি নিক্ষেপ করা যায়, ফলে আশে পাশের মালামাল পানিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।
(৫)রাইজিংমেইন/স্টান্ড পাইপঃ রাইজিং হচ্ছে কোন উচ্চ ভবনে খারাভাবে স্থায়ী পাইপ স্থাপন করে প্রত্যেক তলায় একটি করে পানি সরবরাহে জন্য হোজ সংযোগ পথ রাখা এবং
নীচের তলায় বুষ্টার পাম্প বা ফায়ার পাম্প
দিয়ে পানি সরবরাহ করার জন্য সংযোগ পথ রাখা একটি
স্থায়ী ব্যবস্থা। রাইজিং মেইনকে ২ ভাগে ভাগ
করা হয়েছে। যথা -
(ক)
ওয়েট রাইজারঃ ইহা সয়ংক্রিয় নহে। ৬০ মিটারের উপরে
উচ্চতা সম্পন্ন ভবনে এই ব্যবস্থা থাকবে।
খাড়াভাবে যে পাইপ লাইন
বসান হয় তার মধ্যে
সবসময় পানি ভর্তি থাকে। ওয়েট রাইজার ওয়াটার মেইন এর সাথে কন্ট্রোল
ভাল্ব দ্বারা সংযুক্ত থাকে। ওয়েট রাইজারে একটি বুষ্টার পাম্প এবং ৪৫ কিউবিক মিটারের
জলাধার ভবনের মধ্যবর্তি স্থানে স্থাপন করতে হয়।
(খ)
ড্রাই রাইজারঃ ইহা সয়ংক্রিয় নহে। ১৮ মিটারের উপরে
এবং ৬০ মিটারের নিচের
ভবনে সাধারনত ড্রাই রাইজার ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনে নীচের সংযোগ পথে পাম্প দ্বারা বা ফায়ার সার্ভিস
পানি সরবরাহ দিয়ে উপরে কাজ করেন।
(৬)
স্টীমঃ ইহা সাধারনত জাহাজের খোল, তরলদাহ্য পদার্থে ব্যবহৃত হয়। ওয়েল কোয়েনসিং ট্যাংক, ড্রাইয়ার্স ইত্যাদি পানিতে যে সকল দাহ্য
বস্তু ক্ষতি সাধন করে সেখানে ব্যবহার করতে নেই।
খ।
পানি ছাড়া অন্যান্য নির্বাপন মাধ্যম
(১) ফোম
(লো/হাই)।
(২) কার্বন-ডাই-অক্সাইড।
(৩) ভেপারাইজিং
লিকুইড।
(৪) ড্রাই
পাউডার।
(৫) ইনার্ট
গ্যাস।























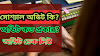







5 Comments
Good post
ReplyDeleteধন্যবাদ স্যার
DeleteKhub valo lagsay
ReplyDeleteধন্যবাদ স্যার
DeleteKhub valo lagsay
ReplyDelete